ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা কতটা প্রস্তুত?
প্রকাশিত:
১২ নভেম্বর ২০২৫ ০৯:৩২
আপডেট:
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ০৯:০৪

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, মহামারি, সড়ক দুর্ঘটনা, বিমান দুর্ঘটনা কিংবা শিল্প দুর্ঘটনা—এসব ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আগেভাগেই প্রস্তুত থাকতে হয়। জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সাধারণত জরুরি ব্যবস্থাপনাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখে—প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ (Preparedness and Prevention), প্রতিক্রিয়া (Response) এবং পুনরুদ্ধার (Recovery)।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আলোকে আবার ভিন্নভাবে ভাগ করা যায়—প্রিকশন [Precaution] (প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি), মিটিগেশন [Mitigation] (ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি) এবং কোপিং [Coping] (প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার)। এই মডেল অনুযায়ী, কার্যকর জরুরি ব্যবস্থাপনা কেবল দুর্ঘটনা-পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম নয়; বরং তার আগে থেকেই ঝুঁকি চিহ্নিত করা, প্রস্তুতি নেওয়া এবং সমাজকে স্থিতিশীল রাখার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।
এই মডেল অনুযায়ী, কার্যকর জরুরি ব্যবস্থাপনা কেবল দুর্ঘটনা-পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম নয়; বরং তার আগে থেকেই ঝুঁকি চিহ্নিত করা, প্রস্তুতি নেওয়া এবং সমাজকে স্থিতিশীল রাখার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।
জাপান, নিউজিল্যান্ড বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় এক ধরনের ‘ঝুঁকি-সচেতন সংস্কৃতি’ গড়ে তুলেছে। জাপানে ভূমিকম্প নিয়মিত হলেও ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম থাকে, কারণ স্কুল থেকে অফিস—সবখানে ভূমিকম্প অনুশীলন বা ড্রিল বাধ্যতামূলক। প্রতিটি নাগরিক জানে, কম্পন শুরু হলে কী করতে হবে, কোথায় আশ্রয় নিতে হবে।
সিঙ্গাপুরে শিল্প নিরাপত্তার অংশ হিসেবে প্রতি ছয় মাসে বাধ্যতামূলক ফায়ার ড্রিল, রিস্ক অডিট ও ইকুইপমেন্ট ইন্সপেকশন করা হয়। ফলে সেখানে দুর্ঘটনা ঘটলেও তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং ক্ষতি সীমিত থাকে। এটি কেবল প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির বিষয় নয়; বরং সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির প্রতিফলন। জরুরি ব্যবস্থাপনাকে তারা ‘পাবলিক সেফটি ইকোসিস্টেম’-এর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে—যেখানে নাগরিক, প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করে।
বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কিছু সাফল্য রয়েছে—বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবিলায়। কিন্তু অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতি—যেমন অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা শিল্প দুর্ঘটনায়—আমাদের প্রতিরোধমূলক ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা এখনো দুর্বল। অফিস, আদালত কিংবা আবাসিক ভবনে এখন ফায়ার এক্সটিংগুইশার (Fire Extinguisher) বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করতে জানেন এমন মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। কারণ এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে কোনো নিয়মিত প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন হয় না।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিজ কক্ষের দরজার পাশেই একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (ফায়ার এক্সটিংগুইশার) ঝোলানো আছে, কিন্তু অগ্নিকাণ্ড ঘটলে আমি সেটি ব্যবহার করতে পারব না—কারণ আমাকে কখনো শেখানো হয়নি কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয়। হয়তো আমার মতো অন্যান্য শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরাও এর ব্যবহার জানে না এগুলোর রিফিল-এর তারিখ প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো রিফিল করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি।
ঢাকার একটি নামকরা হোটেলে একদিন আমি এক কর্মীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘অগ্নিকাণ্ডের সময় আপনি কি এই ফায়ার এক্সটিংগুইশারটি ব্যবহার করতে পারবেন?’ তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ‘হ্যাঁ’ বললেও, যখন আমি জানতে চাইলাম—এর নোজলের মুখে থাকা শক্ত প্লাস্টিকের দড়িটি কীভাবে খুলবেন—তখন তিনি বললেন, ‘এর জন্য তো চুরি বা কাঁচি দরকার হবে।’
আমি তখন প্রশ্ন করলাম, ‘জরুরি অবস্থায়, যখন সবাই আতঙ্কিত, তখন ছুরি বা কাঁচি কোথায় পাবেন, যদি সেটি ফায়ার এক্সটিংগুইশারের সঙ্গেই না থাকে?’ তিনি তখন চুপ করে গেলেন, বললেন—‘আসলে এইভাবে কখনো ভাবিনি।’
এই উত্তরটি আসলে আমাদের সামগ্রিক মানসিকতার প্রতিফলন। ব্যক্তি, সমাজ, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র—কেউই এই বিষয়গুলো নিয়ে আগেভাগে ভাবতে চায় না। আমরা শুধু ফায়ার এক্সটিংগুইশার ঝুলে থাকতে দেখে স্বস্তি পাই বা দেখিয়ে খুশি হই, কিন্তু প্রতিরোধ ও প্রস্তুতির যে সংস্কৃতি—তা এখনো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠেনি।
বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও কাঠামো থাকলেও তা প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যন্ত। কিন্তু আজকের শহুরে বাস্তবতায় প্রধান ঝুঁকি তৈরি করছে অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, পরিবহন দুর্ঘটনা ও শিল্প দুর্ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো—ইন্টিগ্রেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক—যেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রণালয়সমূহ একসঙ্গে কাজ করবে।
এছাড়া জরুরি ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অংশ করা অত্যন্ত জরুরি। যেমন স্কুল পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগ প্রস্তুতি অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করা; সরকারি-বেসরকারি অফিসে বছরে অন্তত একবার ফায়ার সেফটি ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করা; হাসপাতাল, শিল্প কারখানা ও পরিবহন খাতে রিস্ক অডিট সিস্টেম চালু করা; প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জরুরি প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগ করা উচিত।
বাংলাদেশে এই দৃষ্টিভঙ্গি এখনো পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক হয়নি, যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা বৈশ্বিকভাবে প্রশংসিত। উপকূলীয় এলাকায় ‘সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম’ আমাদের সাফল্যের প্রতীক—যেখানে আগাম সতর্কতা, আশ্রয়কেন্দ্র এবং কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে প্রাণহানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একই কাঠামো যখন শিল্প দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড বা মহামারির ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা আসে, সেখানে আমরা এখনো অপ্রস্তুত।
মাইলস্টোন স্কুলের বিমান দুর্ঘটনা, বেইলি রোডের রেস্তোরাঁর অগ্নিকাণ্ড, বনানীর অফিস ভবনে আগুন কিংবা নিমতলি ও রানা প্লাজার মতো ট্র্যাজেডিগুলো স্মরণ করলে আমরা বুঝতে পারি, এই ব্যর্থতার তালিকা কত দীর্ঘ।
প্রতিরোধ মানে ঝুঁকি ঘটার আগেই তা ঠেকানো। কিন্তু বাংলাদেশে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রায়ই ‘ঘটনার পর’ শুরু হয়। ২০১০ সালের নিমতলীর অগ্নিকাণ্ড, ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধস, ২০২১ সালের নারায়ণগঞ্জের হাসেম ফুড ফ্যাক্টরি ট্র্যাজেডি কিংবা ২০২৪ সালের বেইলি রোডের রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ড—সব ঘটনায় একই চিত্র: মৌলিক নিরাপত্তা মানের লঙ্ঘন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং কার্যকর তদারকির অভাব।
বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বলে, প্রতিরোধের মূলভিত্তি হলো নিরাপত্তা সংস্কৃতি—সেফটি কালচার। প্রতিটি পরিবার, স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি সচেতনতা তৈরি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই অনুশীলনের মাধ্যমে শেখে, ভূমিকম্পের সময় কীভাবে নিজেকে ও অন্যকে নিরাপদ রাখতে হয়।
বাংলাদেশেও প্রতিটি স্কুল ও অফিসে বছরে অন্তত একবার ‘অগ্নি ও ভূমিকম্প অনুশীলন’ বাধ্যতামূলক করা গেলে তা প্রতিরোধ পর্যায়ে এক বিপ্লব আনতে পারে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এটি শুরু না হলেও বিকল্পভাবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তায় একটি ‘ওয়েলবিয়িং ক্লাব’ গঠন করে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।
মিটিগেশন ধাপের লক্ষ্য হলো দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন রাখা। এখানে প্রয়োজন অবকাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতা, সঠিক নগর পরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়। ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ভবনের ভেতরে রাসায়নিক গুদাম, সরু গলি এবং ফায়ার সার্ভিসের জন্য প্রবেশের অযোগ্য রাস্তা—সবই ক্ষয়ক্ষতি বাড়ায়।
উন্নত দেশগুলোয় যেমন বিল্ডিং কোড না মানলে ভবন চালু করা যায় না, তেমনি বাংলাদেশেও কার্যকর তদারকি ছাড়া নগর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। চট্টগ্রামের বিএম কনটেইনার ডিপো বিস্ফোরণ কিংবা উত্তরার মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি দেখিয়েছে, নিরাপত্তা প্রোটোকল ও প্রশিক্ষণের অভাবই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। প্রতিটি শিল্প কারখানায় রিস্ক অডিট ও সেফটি ইন্সপেকশন বাধ্যতামূলক করা উচিত এবং স্থানীয় প্রশাসনকে এসব প্রতিবেদন ডিজিটালভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মিটিগেশন অর্থ হলো, সাপ্লাই চেইন প্রস্তুত করা, জরুরি ওষুধ ও সরঞ্জামের মজুদ এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার সক্ষমতা থাকা। কোভিড-১৯ আমাদের দেখিয়েছে, অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের ঘাটতি কীভাবে একটি দেশকে অরক্ষিত করে তোলে। ভবিষ্যতের জন্য তাই প্রয়োজন স্বাস্থ্যখাতে রিস্ক-ইনফর্মড সাপ্লাই চেইন এবং প্রি-পজিশনড স্টক মডিউল, যা এখন বিশ্বব্যাপী জরুরি প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ড।
কোপিং-এর মূল লক্ষ্য হলো ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ, উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকলেও তা সমন্বিত নয়। ফায়ার সার্ভিসের জনবল সীমিত, শহরের ভেতর প্রবেশযোগ্য রাস্তা কম, জরুরি চিকিৎসা নেটওয়ার্কও যথেষ্ট নয়। অনেক সময় ৯৯৯ বা স্থানীয় কন্ট্রোল রুমে ফোন করেও তাৎক্ষণিক সহায়তা পাওয়া যায় না।
বৈশ্বিকভাবে দেখা যায়, সফল কোপিং ব্যবস্থায় তিনটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ—রিয়েল-টাইম ইনফরমেশন, কমিউনিটি নেটওয়ার্ক এবং লিডারশিপ কমিউনিকেশন। যুক্তরাজ্য বা দক্ষিণ কোরিয়ায় জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার একীভূত ‘কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার’ চালু করে, যা রিয়েল-টাইম তথ্য ও উদ্ধার ব্যবস্থাকে একত্র করে। বাংলাদেশেও এ ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করা জরুরি, বিশেষ করে শহুরে অগ্নিকাণ্ড ও শিল্প দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে।
জরুরি ব্যবস্থাপনা কেবল সরকারের কাজ নয়; স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণই বাস্তব সাফল্যের চাবিকাঠি। জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংস্থার (ইউএনডিআরআর) বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ‘কমিউনিটি প্রিপেয়ার্ডনেস’ এখনো দুর্বল। প্রতিটি ওয়ার্ড বা ইউনিয়নে যদি প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় ক্লিনিক, স্কুল ও ফায়ার সার্ভিসের মধ্যে সমন্বিত কমিউনিটি রেসপন্স টিম গঠন করা যায়, তবে প্রতিক্রিয়া অনেক দ্রুত ও কার্যকর হবে। মাদারীপুর ও ময়মনসিংহের কিছু এলাকায় ইতিমধ্যেই কমিউনিটি-বেইজড ডিজাস্টার রেসপন্স টিম কাজ করছে; এই মডেলকে শহরাঞ্চলেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
জরুরি প্রস্তুতির সবচেয়ে বড় উপাদান হলো মানসিক প্রস্তুতি। আমরা প্রায়ই ভাবি, দুর্ঘটনা অন্যের সঙ্গে ঘটে—আমার সঙ্গে নয়। এই উদাসীনতাই আমাদের সবচেয়ে দুর্বল করে তোলে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সচেতনতা, আতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
বিশ্বজুড়ে এখন ‘সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এইড’ ও ‘ক্রাইসিস কমিউনিকেশন’ জরুরি ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশেও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দুর্যোগ-মনোবিজ্ঞান ও দুর্যোগকালীন প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করা যেতে পারে।
জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে—বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে। কিন্তু মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে আমরা এখনো অপ্রস্তুত। এখন প্রয়োজন ‘প্রতিরোধ থেকে পুনরুদ্ধার’—এই পূর্ণচক্রটি সক্রিয় ও সমন্বিত করা। ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা, সমাজ পর্যায়ে অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়—এই তিন স্তরই একে অপরের পরিপূরক।
যদি বাংলাদেশ প্রিকশন, মিটিগেশন ও কোপিং—এই তিন স্তরে সমন্বিত কাঠামো গড়ে তুলতে পারে, তবে আগামী দিনের কোনো নিমতলি, কোনো রানা প্লাজা বা কোনো বেইলি রোড ট্র্যাজেডি হয়তো আর ঘটবে না।
জরুরি পরিস্থিতি কখন ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না; কিন্তু প্রস্তুতি নেওয়া আমাদেরই হাতে। দুর্ঘটনা-পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমে যেমন আমাদের সক্ষমতা বাড়ছে, তেমনই এখন প্রয়োজন দুর্ঘটনা-পূর্ব প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দেওয়া। প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ ও স্থিতিস্থাপকতার সংস্কৃতি যদি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের চেতনার অংশ না হয়, তবে আমরা আগুন, ধস বা দুর্ঘটনার সামনে একইভাবে অসহায় থাকব।
সত্যিকারের প্রস্তুতি তখনই, যখন সমাজ ঝুঁকিকে দেখে ভয় না পেয়ে—তার মোকাবিলার কৌশল জানে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, আগাম প্রস্তুতি ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়া কাঠামো থাকলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।
ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ : অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



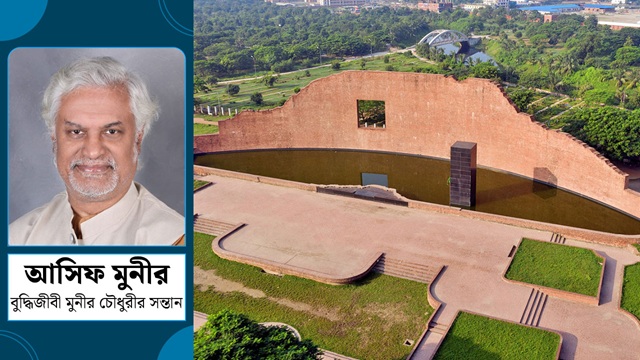

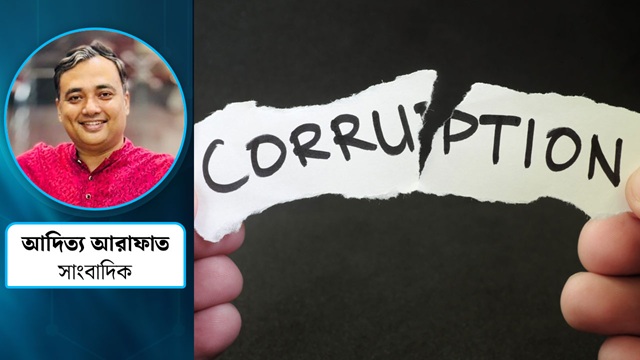



আপনার মূল্যবান মতামত দিন: